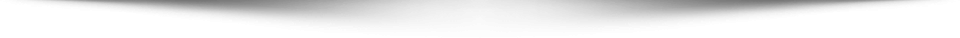- লিটন আব্বাস
[শেষ পর্ব]
নীল বিদ্রোহের শুরু ও কয়েকটি ঘটনা
ঠিক কোথায় প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয় তা নিয়ে নানামত বিদ্যমান। অধিকাংশই মনে করেন, চূর্ণী নদীর তীরবর্তী চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের খাল বোয়ালিয়া ও আসাননগর কুিিঠতে সর্বপ্রথমএই বিদ্রোহ শুরু হয়। কারো মতে, চৌগাছা কুঠিতে এর সূত্রপাত। বাকল্যান্ড সাহেবের মতে, উত্তরবঙ্গে এই বিদ্রোহ শুরু হয়। তার মতে, আওরঙ্গবাদ মহকুমার এন্ড্রোজ কোম্পানির আঙকারা নীলকুঠির ওপর সর্বপ্রথম আক্রমণ করার মাধ্যমে বিদ্রোহ শুরু হয়। তবে বিদ্রোহ যে, বাংলাদেশে শুরু হয়, তা সম্পর্কে সবাই একমত।
তবে সাধারণতঃ বলা হয় যে, অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন মালদহ জেলার কৃষকগণ এবং তা পূর্ণতা সাধন করেন উত্তরবঙ্গের কৃষকেরা। আর সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন টাঙ্গাইলের কাগমারির কৃষকেরা এবং পূর্ণতা সাধন করেন কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গা এলাকার কৃষকগণ।
নীলচাষ প্রতিরোধে শ্রেণীসংগ্রামের যোদ্ধা বিশ্বনাথ সরদার ওরফে বিশে ডাকাত ১৮০১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে স্যামুয়েল ফেডির নীলকুঠি লুন্ঠন করেন। এরপর তার নাম ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাংলায়। বিশ্বনাথ জাতিতে ডোম বা বাগদী ছিলেন- তিনি তিতুমিরের হামকল বাহিনীতে কিশোর বয়সে যোগ দেন। পাঁচবছর প্রশিক্ষণের পর তিনি নিজের গ্রামে ফিরে এসে একদল যুবককে সাথে করে নীলকুঠি দখল ও ধ্বংসের প্রশিক্ষণ দেন এবং নদীয়া জেলার কুনিয়ার জঙ্গলে ঘাঁটি স্থাপন করেন। সেখানে তার সাথে কাহারবা ও অন্যান্য ডাকাতের দল ডাকাতি ছেড়ে যোগ দেয়। তিনি নদীয়ার আশেপাশের বহু নীলকুঠি ও নীলের কারবার ধ্বংন করে দেন। তার এরূপ কর্মকান্ডে জেলা প্রশাসক ইলিয়ট এবং নীলকর ফেডি ভীত হয়ে পড়েন। বিশ্বনাথের মাথার জন্য হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। সরকার ও নীলকরেরা তার নামে তৎকালীন ব্রিটিশ ওয়ান্টেড লিস্টে ‘বিশে ডাকাত’ হিসেবে উঠায়।
১৮০৭ সালে, বিশ্বনাথ কুঠিয়াল ফেডির বাসভবন ও কুঠি আক্রমণ করেন। ফেডির দলের প্রায় সবাই এই অকস্মাৎ আক্রমণে প্রাণ হারায় – বাকিরা পালিয়ে যায়। ফেডির স্ত্রী মাথায় কালো হাঁড়ি চাপিয়ে পুকুরে ডুব দিয়ে প্রাণে বেঁচে যান। বিশ্বনাথের প্রধান সেনাপতি মেঘাই সরকার ফেডিকে বন্দি করে বাগদেবী খালের তীরে নিয়ে আসে। ফেডি বিশ্বনাথের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চায় এবং যিশুর নামে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে ব্যবসা উঠিয়ে ব্রিটেনে চলে যাবে। বিশ্বনাথ তাঁকে ছেড়ে দেন। ফেডি ছাড়া সেদিন দুপুরেই বিশ্বনাথকে ধরিযে দেয়। বিশ্বনাথ দিনাজপুরের জেলে আটক হন। ১৮০৮ সালের ২৭সেপ্টেম্বর জেল থেকে পালানোর ৪ দিন পর বিশ্বনাথ আবার ফেডির ঘরে হানা দেন। তার কোষাগার লুন্ঠন করে ও তার পাইক বাহিনীকে শেষ করে দিয়ে বিশ্বনাথ ফেডির সামনে হাজির হন। কিন্তু এবারো ফেডি নীলচাষ তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রাণ ভিক্ষা চাইলে বিশ্বনাথ এবারো তাকে খুন না করে চলে আসেন। ফেডি এবার বিশ্বনাথের ধ্বংসের জন্য উঠেপড়ে লাগে। সেনাপতি ব্ল্যাকওয়ার ও ব্রিটিশি সেনাবহিনীর একটি দলকে বিশ্বনাথের খোঁজে লাগায়। শুর ুহয় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের প্রথম ম্যানহান্ট। ব্ল্যাকওয়ারের সেনাবাহিনী কুনিয়ার জঙ্গল ঘিরে ফেলে অগ্নিসংযোগ ও গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বনাথ তার অনুচরদের বাঁচাতে নিজে ধরা দেন এবং সমস্ত কর্মকা-ের দায়ভার নিজের ওপরে নিয়ে নেন। ফেডির মুখোমুখি হয়ে বিশ্বনাথ বলেন, ‘গোরা সাহেব, আমি তোমার জুলুম থামিয়ে দিয়ে সংসার জীবনে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। তুমি বাধ সাধলে…’। গঙ্গার তীরভূমিতে বিশ্বনাথকে ফাঁসি দেয়া হয়। তার মৃতদেহ সবাইকে দেখানোর উদ্দেশ্যে লোহার খাঁচায় ঢুকিয়ে একটি অশ্বত্থ গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়। বিশ্বনাথের বিধবা মা ছেলের কঙ্কালটি ভিক্ষা চাইলে অত্যাচরী নীলকররা তাও ফেরৎ দেয়নি! এমনই বর্বর ছিল তারা।
১৮৫৮ সালে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ অসহযোগ আন্দোলনে পরিণত হয় এবং বিদ্রোহ হয়ে বেরিয়ে আসে ১৮৫৯ সালে এপ্রিল-মে মাসে। এর আগেও চাষিরা নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে বারবার।
কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গার সিন্দুরিয়া নীলকুঠির গোমস্তা শীতল বিশ্বাসকে হত্যা করে নীলবিদ্রোহী বিপ্লবী কৃষকপ্রজারা। এছাড়া দুর্গাপুরের পিয়ারি ম-লের রসিক প্রতিবাদ, রব্বানী ম-লের ওপরে অত্যাচার-এর মত ঘটনা নীল বিদ্রোহের অসহযোগ পর্যায়কে আরও বেগবান করে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ প্রশস্ত করে দেয়। এই বিদ্রোহ মূলতঃ ১৮৫৯ সালে, বাস্তব রূপপরিগ্রহ করে ১৮৬০ সালে এবং ১৮৬১ সালে প্রচ- আকার ধারণ করে।
১৮৬০ সালের এপ্রিলে ‘ইন্ডিয়ান ফিল্ড’ নামক মাসিক পত্রিকায় দু’জন জার্মান পাদ্রি চুয়াডাঙ্গার বিপ্লবীদের লঠিয়াল বাহিনী সম্পর্কে লেখেন,
‘অপটু কৃষক যোদ্ধাগণ নিজেদের ৬টি কোম্পানিতে বিভক্ত করেছে। ১ম কোম্পানি তীরন্দাজদের নিয়ে, ২য় কোম্পানি ফিঙা দিয়ে গোলোক নিক্ষেপকারীদের নিয়ে, ইটওয়ালাদের নিয়ে ৩য় কোম্পানি- এরা পরিধেয় লুঙ্গিতে মটির বড়-বড় ঢেলা, ইট-পাটকেল বহন করে এবং ছুঁড়ে মারে। বেলওয়ালাদের নিয়ে ৪র্থ কোম্পানি যাদের কাজ নীলকরদের লঠিয়াল বাহিনীর মাথা বরাবর কাঁচা বেল ছুঁড়ে মারা। থালা-ওয়ালাদের নিয়ে ৫ম কোম্পানি তারা ভাত খাবার কাঁসা ও পিতলের থালাগুলো আনুভূমিকভাবে চালাতে থাকে। এতে শত্রু নিধন যে ভালভাবেই হয় সন্দেহ নেই। ৬ষ্ঠ কোম্পানি মহিলাদের নিয়ে গঠিত। তারা হাতে মাটির পোড়ানো খ-, বাসন ও রুটি বেলার বেলন দিয়ে আক্রমণ করে থাকে। আর যারা পটু, তাদের নিয়ে মূল কোম্পানি গঠিত। এরাই কৃষক লাঠিয়াল, এরা সম্মুখ সমরে অংশ নেয়। এই কেম্পানির অর্ধেক বল্লমধারী,অর্ধেক লাঠিধারী এবং তারপর বাকি ৫টা কোম্পানি। এদের বীরত্ব কিংবদন্তিসম। একজন বল্লমধারী নাকি ১০০জন শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধাকে পরাজিত করতে পারে। সংখ্যায় এরকম হলেও এতোটাই দুর্ধর্ষ যে, তাঁদের ভয়ে নীলকরের লাঠিয়ালগণ পুনরায় আক্রমণ করতে সাহস পেতো না।’
এছাড়া ছিল তিতুমিরের ‘হামকলবহিনী’, এবং ফরায়েজী আন্দোলনের অনুসারীদের ‘দুন্দুভি বাহিনী’র কথাও গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটি বাহিনী ও কৃষক বাহিনীর বিদ্রোহের এজেন্ডা ভিন্ন হলেও এই বাহিনীত্রয়ের লক্ষ্য ছিল একটাই- অত্যাচারী নীলকর ও জমিদারদের ধ্বংস করা। নীল বিদ্রোহে এমন কোনো লড়াই হয়নি, যেখানে হামকল বাহিনী অংশগ্রহণ করেনি…।
সশস্ত্র বিদ্রোহের শুরু ও কয়েকটি ঘটনা
কৃষকেরা অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে নীলচাষে অস্বীকৃতি জানিয়ে হাজার হাজার চুক্তিপত্র পুড়িয়ে ফেলে ও নীলবীজ নদীতে নিক্ষেপ করে। এই অবস্থায় নীলকরররা পুলিশের সাহায্যে হাজার হাজার কৃষককে গ্রেফতার তরে তাঁদের বড়িঘর ক্রোক করে নেয়, ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে শত শত দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। এই অত্যাচারে কৃষক শ্রেণী ফুঁসে ওঠে এবং নীলকরদের ওপর সশস্ত্র পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।
তখন সংবাদপত্রের সংবাদ আদান প্রদানের সুব্যবস্থা না থাকায় কত শত খ- যুদ্ধ যে হয়েছে,তার মাঝে দু’একটার খবর পত্রিকায় এসেছে- যারা খবর ছাপতেন তারাও শ্রেণী স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই বেশিরভাগ পত্রিকা ছাপতেন। তাই এই বিদ্রোহের খুঁটিনাটি বণনণা পাওয়া সম্ভব নয়। এর মধ্যে কয়েকটি আলোচিত ঘটনার উল্লেখ করা গেলো।
বাংলার জোয়ান অব আর্ক পিয়ারি সুন্দরীঃ কুষ্টিয়ার মিরপুরের আমলা সদরপুরের এক নীল বিপ্লবী
টমাস আইভান কেনি তৎকালীন বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মধ্যে সবচে বড় নীল কারবারের অধিকারী ছিল। তার কয়েকটি কুঠি ছিল মিরপুরের আমলা সদরপুরের জমিদারনি পিয়ারি সুন্দরীর জমিদারীর ভেতরে। এই কেনি ছিল অত্যন্ত জুলুমবাজ। হত্যা-ধর্ষণ এগুলো ছিল তার কাছে সামান্য ব্যাপার। তার বিরুদ্ধে ১৮৫০ সালে রায়েতগণ বিদ্রোহ করে। কিন্তু কেনি শক্ত হাতে তা দমন করে এবং সকল রায়েতকে উচ্ছেদ করে নতুন রায়েত বসায়। বাংলার জোয়ান অব আর্ক পিয়ারি সুন্দরী এতে অসন্তুষ্ট হন। তিনি কেনিকে প্রজাদের উচ্ছেদ করার কাজে নিষেধ করেন। এতে কেনি তাঁকে গালিগালাজ করে এবং জমিদারি কেড়ে নেওয়ার ভয় দেখায়। স্বল্পকালীন সময় পিয়ারি অনন্যোপায় হয়ে মৌনব্রত পালন করেন। ১০ বছর পরে ১৮৬০ সালে ওই উচ্ছেদকৃত রায়েতগন সংগঠিত হয়ে ফিরে আসে এবং পিয়ারি সুন্দরী তাঁদের সাথে যোগ দেন। ওই বছরই এপ্রিল মাসে তারা কেনিকে হত্যা এবং তার কুঠি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে কুঠিতে হামলা করেন। কেনি বেঁচে যায়,কিন্তু তার কারবার সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এই হামলা করার কারণে পিয়ারি সুন্দরী ও তার রায়েতদের বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা করা হয়। পিয়ারি সুন্দরী সকল মামলার ব্যয়ভার নিজে বহন করেন,এতে তিনি সর্বশান্ত হয়ে যান। তার পক্ষের প্রজাদের দ্বীপান্তর, জেল, জরিমানা হয় এবং পিয়ারি সুন্দরী সহ সকলের ভূসম্পত্তি বাতিল করা হয়। পিয়ারী তার পাঁচ বছর পর যশোরের এক মুচির বাড়িতে বিনা চিকিৎসায় পরিজনহীন অবস্থায় টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পনের শতকের গোড়ার দিকে ফরাসী বিপ্লবী ও স্বাধীনতা কামী নারী জোয়ান অব আর্ক পুরুষ বেশে ইংল্যা-ের সাথে যুদ্ধ করে মাত্র দেড় বছরেই ফরাসীকে মুক্ত করে রাজা সপ্তম চার্লসের কাছে ক্ষমতা বুঝে দেন। এর ঠিক দুইবছরের মাথায় ইংরেজদের কূটচালে ধরা পড়েন জোয়ান অব আর্ক, তাঁকে ধর্ষণ করে এবং পুড়িয়ে হত্যা করা হয়- এবং হত্যার পর নির্মমভাবে আরো দুইবার পোড়ানো হয়- তাঁর ছাই মিহিদানার মতো উড়ে যায়! ঠিক সেই ফরাসী বিপ্লবী জোয়ান অব আর্কের সাথে তুলনা করে পিয়ারি সুন্দরীকে তুলনা করে ডাকা হয় বাংলার জোয়ান অব আর্ক। অথচ আমরা এই বিপ্লবী পিয়ারী সুন্দরী বাংলার জোয়ান অব আর্ককে ভুলে গেছি! কেনিকে আমরা ভুলিনি। কুষ্টিয়া শহরে কেনি রোডের নামকরণ এই নরপশুর নামে করা!
খন্ড খন্ড কয়েকটি ঘটনা
কেনির মতো দুর্ধষ নীলকর ছিল খুলনার ইলাইপুর নীলকুঠির রেনি। রেনি বি্িরটশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন একজন সৈনিক। ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কারণে রেনি দ্রুত কুখ্যাত হয়ে ওঠে। ১৮৫৫ সালে খুলনা থেকে নীল চাষ প্রবল বিদ্রোহের মুখে উঠে যায়। এরপর ঝিনেদার সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য তাঁর পুত্র অমরনাথকে দুর্ধষ নীলকর ম্যাকনেয়ার গুলি করে হত্যা করে তার পুত্রবধূ সতী আরতি দেবীকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে মথুরানাথ বিপ্লবীদের সাথে একাত্মতাবোধ প্রকাশ করে এবং সরাসরি নীলচাষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তার সাথে ছিল রইস খান, জমিদার শ্রীহরি রায়সহ আরও অনেকে। বিপ্লবী দল ম্যাকনেয়ারের কুঠি আক্রমণ করে আগুন লাগিয়ে দিলে ম্যাকনেয়ারের মেয়ে ইভা আগুনে পুড়ে মারা যায়। ম্যাকনেয়ার নৌকাযোগে পালিয়ে যাবার সময় ধরা পরে এবং মথুরানাথের আদেশে ম্যাকনেয়ারকে নৌকা সহ পুড়িয়ে মারা হয়।
ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় বলা হয়েছে, সর্বপ্রথম ১৮৪৪ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারি নীলকুঠিতে মানুষ খেপে ওঠে এবং আগুনে কুঠিটিকে ভস্মীভূত করে। এভাবে যেখানেই নেতৃত্ব ও সংগঠন গড়ে ওঠে, সেখানেই শুরু হয় প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ।
একরকম হাজার হাজার ঘটনা পুরো বাংলা জুড়েই ঘটতে থাকে। কৃষকেরা রাগে ক্ষোভে পাগল হয়ে ওঠে। সারাদেশের এমন পরিস্থিতি এবং নীলকরদের বেহাল দশা দেখে সরকারের টনক নড়ে। বড় বড় লর্ডেরা বাণী দিতে থাকেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর জন পিটার গ্রান্ট লেখেন,
‘‘শত-সহস্র মানুষের বিক্ষোভের এই প্রকাশ যা আমরা বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ করছি, তাঁকে কেবল একটা রং সংক্রান্ত অতিসাধারণ বাণিজ্য-প্রশ্ন না ভেবে গভীরতম সমস্যা বলেই ভাবা উচিৎ…।’
বড়লাট লর্ড ক্যানিং নীল বিদ্রোহের দুইমাস পরে ইংল্যান্ডে চিঠি লেখেন, ‘নীল চাষিদেরবর্তমান বিদ্রোহের ব্যাপারে প্রায় একসপ্তাহ কাল আমার একই উৎকণ্ঠা হয়েছিল যে, দিল্লির ঘটনার (১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ) সময়ও আমি এতোটা চিন্তিত হই নি। আমি সবসময় চিন্তা করেছি যে, যদি কোন নির্বোধ নীলকর ভয়ে বা ক্রোধে একটি গুলিও ছোঁড়ে, তাহলে সেই মুহূর্তেই দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত কুঠিতে আগুন জ্বলে উঠবে।’
নিজেরা রক্ষা পেতে ১৮৬০ সালের মার্চ মাসে বাংলার লেফটেন্যান্ট গর্ভনরের কাছে স্মারকপত্র দেয় এবং জানায় যে, কৃষককুল সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে- তাঁদের দিয়ে আর নীলের আবাদ করানো সম্ভব হচ্ছে না…রায়েতরা বর্তমানে খুবই মারমুখি। তারা ভংঙ্করভাবে ক্ষেপে গেছে।
নীলচাষের অন্তিমকালঃ ইন্ডিগো কমিশন গঠন
১৮৬০ সালের ৩১ মার্চ নীল কমিশন বা ইন্ডিগো কমিশন গঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন বঙ্গীয় সরকারের সেক্রোটরি M.W.S. Seaton Carr কমিশনের একজন বাদে সবাই ছিলেন ইংরেজ। বাকি ওই একজন ছিলেন জমিদার সমিতির এক সদস্য। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে কমিশনের প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৬০ সালের ১৮ মে। কমিশন ৩ মাসে ১৩৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। সাক্ষীদের মাঝে ছিল ১৫ জন সরকরি কর্মচারি, ২১জন নীলকর, ৮ জন মিশনারী, ১৩ জন জমিদার ও ৭৯ জন নীলচাষি।
দীর্ঘ আলোচনা শেষ কমিশন রিপোর্ট দেয়, The whole system is vicious in theory, injurious in practice and radically unsound.
কমিশনের রিপোর্ট ও ছোটলাটের স্বীকৃতি সত্বেও সরকার রায় দেয় নীলকরদের দিকেই। সরকার নিজেকে নিরপেক্ষ ঘোষণা করে,কিন্তু নীলকরদের নিরাপত্তার জন্য পূর্বের সকল দমন মূলক আইন বজায় রেখে নতুন নতুন থানা ও মহকুমা স্থাপন করে পুলিশের শক্তি বাড়াতে থাকে যাতে সহজেই বিদ্রোহ দমন করা যায়। সেই সাথে কৃষকদের সান্ত¡না দিতে কয়েকটি অর্থহীন ইশতেহার জারি করা হয়-
১. সরকার নীলচাষ করার বিষয়ে নিরপেক্ষ। ২.আইন অমান্য করলে বিদ্রোহী প্রজা বা নীলকর কেউই শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। ৩. অন্য শস্যের মতো নীলচাষ করা বা না করা প্রজার ইচ্ছাধীন।
সরকারের এ প্রতারণা কৃষকেরা বুঝতে পারে। নদীয়া ও যশোরের কৃষকেরা হেমন্তকালীন নীলচাষ করা এবং জমিদার ও নীলকরদের খাজনা দেয়া বন্ধ করে দেয়। এই কর্মতৎপরতা থামাতে সরকার দুইজেলাই দুই দল সৈন্য রণতরী পাঠায়। দুইদলের অধিনায়কের সাথে কৃষকজনতা আলোচনায় বসে প্রজারা বলে, ‘খাজনা দিতে আপত্তি নেই,তবে নীলকর ও জমিদারদের নির্যাতন হতে প্রজাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে। অধিনায়ক দু’জন ফিরে গিয়ে ছোট লাট গ্রান্টকে অবহিত করলে; গ্রান্ট স্বচক্ষে অবস্থা দেখতে ১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে স্টিমার যোগে গোপনে দীর্ঘ ৭০ মাইল জলপথে ১৪-১৫ ঘন্টার যাত্রা শুরু করলে প্রজারা জানতে পরে লক্ষ-লক্ষ কৃষক প্রজা নদীরে দুইধারে দাঁড়িয়ে থাকে। গ্রান্ট ভয় পেলে কৃষকরা বোঝাতে সক্ষম হয় এবং অভয় দিলে গ্রান্ট কৃষকদের কথা শুনে তাদেরকে পাবনা যেতে বলেন। গ্রান্ট বলেন, সেখানে জনসভায় তিনি নীলচাষ তুলে দেবার ঘোষণা দেবেন।
পাবনার জনসভায় গ্রান্ট বলেন, ‘অতিশীঘ্রই নীল চাষ বন্ধের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চাষির ইচ্ছা ব্যতিত, কাউকে জোর করে নীলচাষ করানো যাবে না। কেউ জোর করে নীলচাষ করালে আইন কঠোর হাতে তাঁকে দমন করবে’।
গ্রান্টের কথা উপেক্ষা করে নীলকররা তাঁদের সমিতি ইন্ডিগো প্ল্যানটার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর ক্ষমতার জোর খাটিয়ে নীলচাষ বন্ধের যে আইন প্রণীত হবার কথা ছিল,তা রদ করে দেয়।
এতে গ্রান্ট বিক্ষুব্ধ হয়ে বিবৃতি দেন, ‘ আইনের বিপক্ষে, নীলচাষের সপক্ষে পৃথিবীর কোন শক্তিই আর বেশিদিন এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারবে না। ন্যায়ের পথ উপেক্ষা করে যদি সরকার চলতে থাকে, তবে আরও বিপুল কৃষক অভ্যুত্থান ও বিপ্লব সরকারের শাস্তি বিধান করবে’।
এইসব সত্যি হয়ে দেখা দেয় ক’বছরের মধ্যে। যারা জুলুমবাজ নীলকর ছিল, বিপ্লবের মুখে তারা ব্যবসা গুটিয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হয়, নইলে কৃষকদের সাথে যুদ্ধে প্রাণ হারায়।
ব্যতিক্রম ছিল কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গার সিন্দুরিয়া কুঠির ম্যানেজার ড্যাম্বেল পিটারস। সে এই সকল বিদ্রোহে খেপে গিয়ে আরও বেশি অত্যাচার শুরু করে।ওই স্থানে পুলিশের সংখ্যা বেশি ছিল বলে কৃষকরা প্রতিবাদ করতে গেলে বিপদে পড়তে হতো। বাংলার প্রায় সকল জায়গায় নীল চাষ বন্ধ হয়ে গেলে এবং কৃষকরা আরও সংগঠিত হয়ে কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গা কুঠির দিকে দলেদলে আসতে থাকে। এরই ফল হিসাবে ১৮৮৯ সালে কুষ্টিয়ার চুয়াডাঙ্গার সিন্দুরিয়ায় সর্বশেষ নীলবিদ্রোহ হয়। ফলস্বরূপ নীলচাষ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এই বিদ্রোহে সর্বপ্রথম অভিজাত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কৃষকদের সমর্থণ করেন। সিন্দুরিয়ার বিদ্রোহ ছিল সর্বশেষ নীল বিদ্রোহ। এরপরে বাংলার আর বিদ্রোহ হয়নি করার দরকারও হয়নি।
নীলচাষ ও বিদ্রোহ গেলেও তাঁর চিহ্নস্বরূপ এখনো বাংলার আনাচেকানাচে সেইসব নীলকুঠির ভগ্নচিহ্ন রয়ে গেছে। যা থেকে শিক্ষা নিতে বলে ইতিহাস! পরিতাপের বিষয় যে, ঘঠনা ঘটে যাওয়ার পর শিক্ষা নেয় বিশেষত বাঙালি সমাজ। অথচ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিলেপরবর্তীতে এবং পরমপরা ঘটে যাওয়া নির্মম ঘটনাগুলো আর ঘটতো না। তাই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া সকলেরই উচিত।
কৈফিয়ৎ-১: নীল চাষ ও বিদ্রোহের সঠিক ইতিবৃত্ত জানতে প্রোফেসর শঙ্কুর ব্লগে যা বর্ণিত আছে তা সংক্ষিপ্ত অথচ সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্যে ভরপুর। তিনি ৫৯টি রেফারেন্স, ৮টি লিংক এবং আরও ২৫জনের মতামত সম্বলিত তাঁর এই গবেষণালব্ধ লেখা পাঠ করলে বাংলার নীলচাষ-এর সঠিক ইতিহাস জানা সম্ভব। তিনি যে তথ্যপুঞ্জির উল্লেখ করেছেন এবর্ং দীর্ঘদিন গবেষণা করে একটি মজবুত ভিত্তির ওপর তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশ করে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ,গবেষকদের কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছেন। নীল আন্দোলন, চাষ নিয়ে অন্তর্জালে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধে, গ্রন্থে একেক জায়গায় একেকরকম – এইসকল হেরফের লেখা দীর্ঘ ৮/১০ বছর পাঠ করে এবং নেটিজেনে উইকপিডিয়া, অনলাইন পোর্টাল দেখার পর, সামহোয়ার ব্লগ থেকে প্রোফেসর শঙ্কুর এই লেখাটিকে সঠিক এবং অধিক গ্রহণীয় বলে প্রতীমান হয়।
তথ্য ঋণ:
- প্রফেসর শঙ্কু/ ‘নীল বিদ্রোহঃ বাংলার সর্বপ্রথম সফল বিদ্রোহ’; লিংক: https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/professorShonku/29821728
- মুহম্মদ ইউসুফ হোসেনঃ ‘নীল বিদ্রোহের নানা কথা’ পৃঃ ১৭,১৯,৩১, ৪৮, ৯৩
- প্রমোদ সেনগুপ্তঃ ‘নীধ বিদ্রোহ ও বাঙ্গালি সমাজ
- সুপ্রকাশরায়ঃ ‘ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।
- শ.ম. শওকত আলী- কুষ্টিয়ার ইতিহাস
- নীল কশিনের সামনে তারাচাঁদ মন্ডলের স্বীকারোক্তি।
- মাধ্যমিক সমাজ বিজ্ঞান (শিক্ষাবর্ষ ২০১০), পৃঃ৪৭-৪৮
- C.E. Buckland: Bengal under the Lieutenant Governors
- Major Smith:Report on the Maldah
- W. Hunter: Imperial Gazetteer of India
- Calcutta review. Vol. 36. p.40
- James Watts: Dictionary of Economy Products of India.
- Indigo Comission Report, Evidence,p.32
- Calcutta Review,Nov. 1860